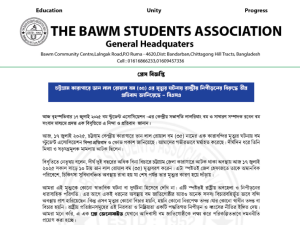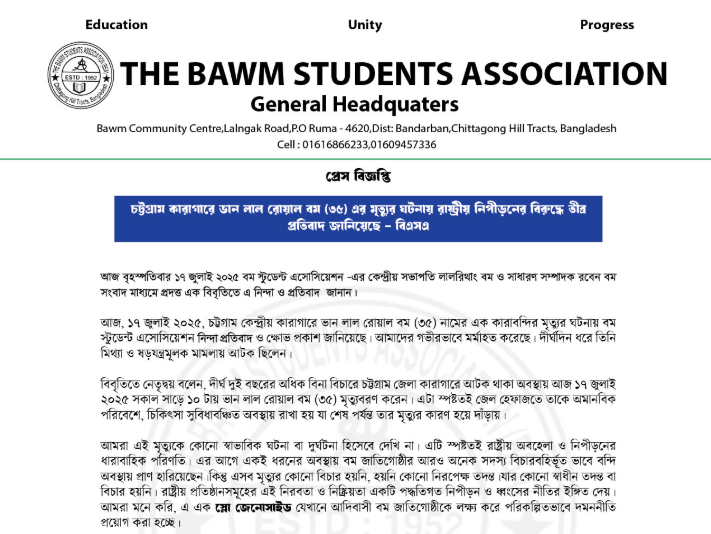৪র্থ অংশ: আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সশস্ত্র আন্দোলন
মঙ্গল কুমার চাকমা
এম এন লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একের পর এক দাবি-দাওয়া পেশ সত্তে ও জুম্ম জনগণের কোন দাবি-দাওয়াই তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার আমলে নেয়নি। এমতাবস্থায় জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রাম করে এই উগ্র ধর্মান্ধ ও সম্প্রসারণবাদী সরকারের কাছ থেকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করা সম্ভব হবে না। এজন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই বলে জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির অনুভব করতে থাকে। তাই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি ধীরে ধীরে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেরও প্রস্তুতি নিয়ে থাকে জুম্ম জনগণ। যার চুড়ান্ত ফল হিসেবে ১৯৭৩ সালে ৭ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে গঠন করা হয় সশস্ত্র শাখা ‘শান্তিবাহিনী’।
দলে দলে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতা-কর্মীরা শান্তিবাহিনীতে যোগ দিতে থাকেন। তৎসময়ে পার্বত্যাঞ্চলের অন্যতম বিদ্যাপীঠ রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতির মূল কেন্দ্র। শান্তিবাহিনীতে তথা সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেয়া অধিকাংশ ছাত্র নেতৃবৃন্দ ছিলেন রাঙ্গামাটি কলেজের শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া বাদ দিয়ে কিংবা সন্নিকটস্থ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেন। এভাবেই শত শত জুম্ম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া শেষ না করে যোগ দিয়েছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনে। সেই সাথে জুম্ম জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করতে থাকে। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির এই বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী মহাসিদ্ধান্ত অচিরেই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সশস্ত্র আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয় সরকারি বাহিনীর উপর শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ। সেসময় ছিল যুব সমাজের মধ্যে আলোড়িত করে শান্তিবাহিনীতে তথা সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেয়ার এক প্রচন্ড জোয়ার। তার ফলে সেসময় শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারে দাঁড়িয়েছিল।
রাজাকার, মুজাহিদ ও মিজো দমনের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরীহ ও নিরপরাধ জনগণের উপর চলতে থাকে সরকারের দমনমূলক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সরকারি প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। ধরপাকড়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ডাকাতি, রাহাজানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে পড়ে। এ সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য সশস্ত্র ডাকাত দল গড়ে উঠে। সশস্ত্র ডাকাত দলের কাছে গ্রামের মানুষ জিম্মি হয়ে পড়ে। চোর-ডাকাতের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল জুম্মদের জনজীবন। মানুষের জানমালের কোন নিরাপত্তা ছিল না। চরম ভয়-আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষজনের দিনাতিপাত করতে হতো। তাই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রারম্ভেই জনসংহতি সমিতির সশস্ত্রবাহিনীকে সেসব ডাকাত দল ও সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত করতে হয়েছিল। স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করে ডাকাত দল ও সশস্ত্র গ্রুপের বিরুদ্ধে গণজোয়ার সৃষ্টি করে এলাকায় এলাকায় ডাকাত দল ও সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের আটক করা হয় এবং শাস্তি বিধান করে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। এভাবে ডাকাত দল ও সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের দমন করার ফলে এলাকায় এলাকায় মানুষের জীবনে শান্তি চলে আসে। মানুষ হাফ ছেড়ে বাঁচে। জনজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যদেরকে শান্তিবাহিনী বলে ডাকতে শুরু করে। এভাবেই জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখার নাম ‘শান্তিবাহিনী’ নামকরণ হয়ে থাকে।
প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র দলগুলোর সাথে সংঘাত
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সহজ পথে এগোয়নি। জন্মলগ্ন থেকেই দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী মহল বরাবরই জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, আপোষপন্থীদের কাছ থেকে বাধা পেতে থাকে। ফলে মোকাবেলা করতে হয়েছিল ১৯৭৩ সালে পংকজ দেওয়ানের নেতৃত্বে চাকমা রাজ পরিবাদের সদস্যদের নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি যুব সংঘ, ১৯৭১ সালে গঠিত ট্রাইবাল পিপলস পার্টি (টিপিপি), পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি ও তার সহযোগী সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম গণমুক্তি পরিষদ, মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ), বোমাং রাজ পরিবারের বামাঞাতা গ্রুপ, রাকাপা প্রভৃতি প্রতিবিপ্লবী সশস্ত্র গ্রুপকে।
সশস্ত্র আক্রমণের মাধ্যমে কোণঠাসা হলে শেষ পর্যন্ত এসব সশস্ত্র গ্রুপগুলো নিশ্চুপ হতে বাধা হয়েছিল। আরো মোকাবেলা করতে হয়েছিল সরকারের মদদপুষ্ঠ ট্রাইবাল কনভেনশনের মতো সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রও। শুধু তাই নয়, এসব সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল মহল দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জনসংহতি সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের চরম বিরোধিতা করেছিল। এসব সশস্ত্র সংগঠনের প্রতিবিপ্লবী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে বিচক্ষণতার সাথে লড়াই-সংগ্রাম করে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল।
সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থা
সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালে জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংগঠিত করা; আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সামিল করা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। এই সরকার ব্যবস্থার বেসমারিক প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক বিভাগ, প্রথাগত আইনী ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যকর ছিল। সমান্তরাল সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থা জনসংহতি সমিতির নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সর্বনিম্নস্তর ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। জুম্ম জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে সামিল করা, জুম্ম সমাজে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করা, শাসনব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ছিল এক যুগান্তকারী উদ্যোগ। জনসংহতি সমিতির এই সমান্তরাল সরকারব্যবস্থার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।
যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার সময় তার এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে জুম্ম যুব সমাজকে সামিল করার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ করে। যুব সমাজকে সশস্ত্র আন্দোলনের মজুদ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রারম্ভে অধিকার সচেতন, অগ্রগামী ও সক্রিয় ছাত্র-যুবকদের বাছাই করে শত শত যুবককে সংক্ষিপ্ত সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। এভাবে গড়ে তোলা হয় সশস্ত্র আন্দোলনের এক বিরাট মিলিশিয়া বাহিনী। এই মিলিশিয়া বাহিনীকে পেছনে মজুদবাহিনী হিসেবে প্রস্তুত রাখা হতো এবং প্রয়োজন মতো তারা যুদ্ধের ময়দানে, গণসংগঠনে ও আন্দোলনের যে কোন কাজে কর্তব্য পালন করতেন।
গ্রামে গ্রামে যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজকে দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ও প্রগতিশীল নীতি-আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে যুব সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সমাজ বিকাশের বৈপ্লবিক আন্দোলনে সমাবেশ ও সক্রিয় করার মানসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করা হয়। সত্তর দশকে অধিকাংশ ছাত্র-যুব সমাজ কোন না কোনভাবে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।
জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সামিল করার লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম হাতে নেয়। নারীর অধিকার ও এই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণার মধ্য দিয়ে জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সামিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে জুম্ম নারী জাগরণ সংঘবদ্ধ ও জোরালোভাবে শুরু হয়। জুম্ম নারীদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী নারী সংগঠন গঠনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। ১৯৭৩ সালের প্রারম্ভে এক পর্যায়ে মহিলা সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অগ্রগামী জুম্ম নারীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হতে থাকে। অবশেষে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ সালে খাগড়াছড়ির ইটছড়ি গ্রামে এক মহিলা সম্মেলন আয়োজন করা হয় এবং সেই সম্মেলনে “পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি” নামে জুম্ম নারীদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম নারী সমাজের জন্য আরো একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হয়। ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সদস্যদের প্রথম রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। ৩৫ জন সদস্য ঐ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ কোর্সও শুরু হয়েছিল। জুম্ম নারীদের এটাই প্রথম সামরিক প্রশিক্ষণ।
মহান নেতা এম এন লারমার প্রদর্শিত নীতি-আদর্শের আলোকে জনসংহতি সমিতির গণলাইনই ছিল পার্টির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের সশস্ত্র আন্দোলনের রাজনৈতিক ভিত্তি। জনগণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা, পার্টি সংগঠনের গুণমান বৃদ্ধি করা, জনগণের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার ভিত্তি ছিল এই গণলাইন। সরকারি বাহিনীর অব্যাহত দমন-পীড়নের মুখেও আন্দোলন থেকে যাতে জনগণ সরে না পড়ে তজ্জন্য গণমানুষের সাথে সংযোগ রাখতে হতো। সশস্ত্র আন্দোলনে জনসংহতি সমিতি কখনোই অস্ত্রকে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেনি। গণসংগঠনকেই সবচেয়ে বড় শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন পার্টি নেতৃত্ব। এভাবেই গণলাইনের মাধ্যমেই নির্মিত হয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলনের ইস্পাত-কঠিন রাজনৈতিক ভিত্তি। এই গণলাইনই সশস্ত্র আন্দোলনের সময় সরকারি বাহিনী নির্মম দমন-পীড়নের মুখেও জনসংহতি সমিতি ও কর্মীবাহিনীকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করাতে পারেনি। সশস্ত্র আন্দোলনের সময় জনসংহতি সমিতির যুগান্তকারী গণলাইনের আরেক রূপ ছিল যোগাযোগ লাইন। মাঠ পর্যায়ে গণলাইনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে নিপারদে চিঠিপত্রও আদান-প্রদান করা হতো। সশস্ত্র আন্দোলনের সময় কাট্টন্যা সমিতি, মংস্যজীবী সমিতি ইত্যাদি অনেক গণসংগঠন সক্রিয় ছিল।
সন্তু লারমাকে গ্রেফতার
১৯৭৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দুইজন সহযোদ্ধাসহ জনসংহতি সমিতির বিপ্লবী নেতা ও সশস্ত্রবাহিনীর ফিল্ড কম্যান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার কুকিছড়া নামক স্থানে টহলরত পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সন্তু লারমা ও তার সঙ্গীদের প্রথমে ৫৪ ধারায় সন্দেহভাজন হিসেবে, পরে ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার দেখানো হয়। সশস্ত্র আন্দোলনের প্রারম্ভেই সন্তু লারমার গ্রেফতার জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে বড় ধরনের ধাক্কা আসে।
জেলে অন্তরীণ থাকাকালে তাঁর উপর নৃশংস শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তা সত্তে ও তিনি জেলে অন্তরীণ অবস্থায় জেলবন্দী বিভিন্ন জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য প্রচারনা চালান। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে জেলে বসে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন সন্তু লারমা। গোপনে বিভিন্ন দৈনিকে পাঠানো হলে দু’টি প্রবন্ধও পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রায় সাড়ে চার বছর জেলে অন্তরীণ থাকার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের স্বার্থে ১৯৮০ সালে ২২ জানুয়ারি রাঙ্গামাটি থেকে নি:শর্তে মুক্তিলাভ করেন। তাঁর সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন বিভূতি চাকমা, চাবাই মগ ও জনৈক ত্রিপুরা কর্মী।
বিরাজমান পরিস্থিতিতে এম এন লারমা সন্তু লারমাকে নির্দেশ দেন বাইরে না থেকে হেডকোয়ার্টারে যোগদান করতে। ফলে ১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল সন্তু লারমা পরিবার-পরিজন নিয়ে আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। এসময় সন্তু লারমাকে পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করে নির্বাহী ক্ষমতা দিয়ে এক পত্রযোগে হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করেন এম এন লারমা। এভাবেই মুক্তিলাভের পর তিনি আবার সশস্ত্র আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পার্টির কার্যকরী সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
জনসংহতি সমিতির ২য় জাতীয় সম্মেলন ও বিভেদপন্থী চক্রের উপদলীয় চক্রান্ত
যুগে যুগে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আন্দোলনে কখনো হয়েছিল বিপ্লবী সংগ্রামী, আবার কখনো হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী। জুম্ম জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনেও প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী চিন্তাধারার লোকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে পার্টিতে কাজ করে আসছিল। পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী, দুর্নীতিবাজ ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তাবেদার ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) ও ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্রও তাদের হীন মুখোশ পার্টির মধ্যে বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। জনসংহতি সমিতির ১৯৭৭ সালে প্রথম জাতীয় সম্মেলনে এই সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানীদের সেই মুখোশ উন্মোচিত করতে চেষ্টা করলেও কর্মীবাহিনীর ঐক্য-সংহতির মুখে তারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তবে সে যাত্রায় তারা ব্যর্থ হলেও তার পরবর্তী থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শিবিরের শক্তি বৃদ্ধিতে ‘পঞ্চম বাহিনী’র ভূমিকা পালন করতে থাকে। তাই দেশী-বিদেশী গুপ্তচরের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে চার কুচক্রী এই জুম্ম জাতির সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়। শুরু হয় উপদলীয় চক্রান্তের আনুষ্ঠানিক পাঁয়তারা। শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গতিপথে ক্রমাগত উদ্যোগশক্তির ভাটা পড়তে থাকে লক্ষনীয়ভাবে।
১৯৮২ সাল জুম্ম জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ বছর। এই বছরে এতদিনে লুকিয়ে থাকা সেই প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চাভিলাষী হয়ে, সর্বোপরি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গুপ্তচর, দালাল ও ফক্করদের চক্রান্তে জড়িত হয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ১৯৮২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপদলীয় চক্রান্তকারীরা পার্টির নীতি ও কৌশল তথা নেতা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থাপন করে থাকে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। বিভেদপন্থীদের চক্রান্ত সত্তে ও এম এন লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনেও তৃতীয়বারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে এম এন লারমাকে পার্টির সভাপতি পদে পুন:নির্বাচিত করা হয়।
কিন্তু ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সম্মেলনের রায় মেনে নিলেও চক্রান্তের নাটক এখানে শেষ করেনি। সম্মেলনের পর এরা আবার নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অতি সঙ্গোপনে, গোপন বৈঠকে তারা জনসংহতি সমিতির সমান্তরাল আরেকটি পার্টি সৃষ্টি করে সেখানে একটি নয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। এভাবে উপদলীয় কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে লাগলো। তার বহি:প্রকাশ হলো ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি। চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারূদ যখন সরিয়ে ফেলতে থাকে। তখন ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন কেন্দ্রীয় অনুগত বাহিনীর সাথে চক্রান্তকারীদের উস্কানীতে পানছড়ি থানার গোলকপদিমাছড়ার লাম্বাছড়ার উৎসমুখে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এভাবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। পার্টির সভাপতি এই সময়ে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেতে থাকেন। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহস, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতায় এই গৃহযুদ্ধ অবসান করানোর উদ্যোগ নেয়া হলো।
এম এন লারমার সভাপতিত্বে ১৯৮৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভেদপন্থীদের সাথে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ‘ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা’ নীতির ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু জুম্ম জাতীয় কুলাঙ্গার, উচ্চাভিষাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের কালি শুকোতে না শুকোতে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ প্রিয় নেতা এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১০ই নভেম্বরের ঘটনার ফলে গৃহযুদ্ধ এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়।
১০ নভেম্বরের নৃশংস ঘটনার পর পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে নির্বাচিত করা হয়। বিভেদপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক সশস্ত্র আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমাকে নৃশংস হত্যার পর গর্জে উঠে দেশপ্রেমিক কর্মীবাহিনী ও আপামর জুম্ম জনতা। পার্টি ও জনগণ আবারো একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন প্রতিঘাত দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। ফলে বিভেদপন্থীরা ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে শত শত জনতার সামনে অতি নির্লজ্জভাবে শত্রুর কাছে সশন্ত্রভাবে আত্মসমর্পন করে। তার মধ্য দিয়ে বিভেদপন্থীদের চক্রান্ত তথা অনাকাঙ্খিত গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
একদিকে সরকারের দমন-পীড়ন, অন্যদিকে জুম্ম জনগণের দুর্বার সশস্ত্র আন্দোলন
একদিকে জনসংহতি সমিতি যখন তার বৈপ্লবিক কর্মসূচি অনুসারে অগ্রসর হচ্ছে, অপরদিকে বাংলাদেশ সরকারও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বাধীন জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দমন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে থাকে। শাসকশ্রেণি এই সংগ্রামকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সত্তর দশকে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে না দেখে বরং অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে সমাধানের উদ্যোগী হয়। তদুদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ২০ অক্টোবর এক অধ্যাদেশের (৬৭নং অধ্যাদেশ) মাধ্যমে গঠন করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড। এই বোর্ডের মাধ্যমে উন্নয়নের নামে কাউন্টার ইনসারজেন্সী কার্যক্রম হাতে নেয়া হতে থাকে। সেনাবাহিনী চলাচলের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক হারে সড়ক ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনজ সম্পদ পাচারের পথ সুপ্রশস্থ হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়।
জনসংহতি সমিতিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন বা জুম্ম জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য সরকার ১৯৭৭ সালের ৪ জুলাই সৃষ্টি করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ও সরকারি দালাল সংস্থা ‘ট্রাইবাল কনভেনশন’। এই ট্রাইবাল কনভেনশনকে পরিচালনা করতো সেনাবাহিনী। ট্রাইবাল কনভেনশনের জনসভায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে হেডম্যান-কার্বাবী, জনপ্রতিনিধি ও এলাকার মুরুব্বীদের উপস্থিত হতে বাধ্য করা হতো। হেডম্যান-কার্বারী ও জনপ্রতিনিধিদের জনসভায় যোগ না দিলে আখ্যায়িত করা হতো দুষ্কৃতিকারী, শিকার হতে হতো জেলজুলুমের। আশেপাশে গ্রামগুলোতে গিয়ে সেনাবাহিনী গ্রাম ঘেরাও করে জনসাধারণকে জোর করে উপস্থিত করা হতো জনসভায়।
পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে স্থাপন করা হয় তথাকথিত আদর্শ গ্রাম ও যুক্ত গ্রাম। আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সাল থেকে জুম্ম জনগণের জীবন-জীবিকার সাথে বিরোধাত্মক যৌথ খামার, আদর্শগ্রাম, বড়গ্রাম ও শান্তিগ্রাম নামে একপ্রকার কারা শিবিরে জুম্মদের বন্দী করা হয়। সামরিক বাহিনী জুম্ম জনগণের বংশ পরম্পায় বসবাসরত গ্রামগুলো ভেঙ্গে দিয়ে জোর করে নিয়ে এনে এক জায়গায় একত্রিত করতো অনেক গ্রামের লোকজন। এসব নিষ্ঠুরতম কাজের দ্বারা বাংলাদেশ সরকার জনগণ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পুরো গণবিরোধী সরকারে পরিণত হয়ে পড়ে।
“১৯৮০ সালের উপদ্রুত এলাকা বিল” প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপদ্রুত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামে গণহত্যা, পাইকারী হারে গ্রেফতার, সীমাহীন নির্যাতন ও উৎপীড়নের পথ উন্মুক্ত হয়। এরশাদ শাসনামলে জুম্ম জনগণের উপর ষড়যন্ত্রের রূপ আরো ভয়াবহ ও নগ্ন হয়ে উঠে। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার জন্য ১৯৭৯ সালে স্বৈরাচারী জিয়া সরকার সমতল জেলাগুলো থেকে মুসলমান বসতিপ্রদানের জঘন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বহিরাগতদের বসতি প্রদান এবং সেটেলারদেরকে অবৈধভাবে ভূমিস্বত্ব প্রদানের হীনউদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে জেনারেল জিয়া সরকার ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ এর ৩৪ ধারা সংশোধন করে।
পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ বিস্তারের উদ্দেশ্যে সামরিক সরকার একদিকে লক্ষ লক্ষ বাঙালি মুসলমানকে বেআইনীভাবে বসতি প্রদান করতে থাকে ও তাদের দিয়ে জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল করা হতে থাকে, অমানুষিক নির্যাতন-নিপীড়ন চালাতে থাকে এবং তথাকথিত উন্নয়নের নামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে আঘাত করতে থাকে; অন্যাদিক জুম্ম জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিহানি করতে থাকে। এর ফলে নিজেদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয় জুম্ম জনগণ। মুজিব সরকারের গৃহীত পলিসি জিয়া সরকার এবং জিয়া সরকারের পলিসি এরশাদ সরকার অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।
নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে জুম্মদের চিরতরে নিশ্চিহ্নকরণের লক্ষ্যে বহিরাগত সেটেলারদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর কমপক্ষে ১৫টি গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। এসব গণহত্যায় শিশু ও নারী শত শত মানুষ নৃশংসভাবে নিহত হয়। গ্রামের পর গ্রাম ভস্মিভূত হয়। হাজার হাজার মানুষ নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। তম্মধ্যে দফায় দফায় জুম্মরা ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়ে বাধ্য হয়। এছাড়া প্রায় এক লক্ষ জুম্ম পরিবার নিজ গ্রাম ও মৌজা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। খাগড়াছড়ি জেলার জুম্ম শরণার্থীদের ভূমি দলিলপত্রাদি ধ্বংস করার লক্ষ্যে ও সেটেলার বাঙালিদের নামে দেয়া অবৈধ কবুলিয়ত বৈধতা দানের হীনউদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে খাগড়াছড়ি জেলাবাসীর একমাত্র ভূমি অফিসকে অগ্নিসংযোগ করে সকল ভূমি দলিলপত্রাদি ধ্বংস করা হয়।
সরকারের দমন-পীড়নের এসব ধ্বংসাত্মক ও ফ্যাসীবাদী পদক্ষেপ কার্যকর হওয়া সত্তে ও জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে বানচাল করা সম্ভব হয়নি। সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। মুক্তি পাগল জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতি আরো বেশি মজবুত হতে থাকে। যতই সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন নৃশংস রূপ লাভ করতে থাকে, ততই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। সরকারি বাহিনীর উপর জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর একের পর এক সশস্ত্র আক্রমণ সংঘটিত হতে থাকে। অপরদিকে দেশে-বিদেশে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক সমর্থন বৃদ্ধি হতে থাকে।
জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কৌশলগতভাবে বন্ধু গড়ে তোলা ও সাহায্য চাওয়ার নীতি-কৌশল গ্রহণ করে। তারই আলোকে আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য জনসংহতি সমিতি উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইউরোপসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গণে জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র হিসেবে ড. রামেন্দ্র শেখর দেওয়ান (আর এস দেওয়ান) সত্তর দশক থেকে জুম্ম জনগণের আন্দোলনের পক্ষে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা ও জনমত গঠনের কাজ চালাতে থাকেন। তিনি যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিয়ানের পত্তন ঘটিয়ে ধীরে ধীরে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেন।
আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের অন্যতম অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার বিরোধী ও সন্ত্রাসমূলক হীন কার্যক্রমের গভীরতা ও সঠিকতা নিরূপনের জন্য গঠিত হয় একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (সংক্ষেপে সিএইচটি কমিশন)। এই কমিশন ২১ নভেম্বর ১৯৯০ থেকে পাঁচ দিনব্যাপী ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরার জুম্ম শরণার্থী শিবিরগুলো এবং ৮ ডিসেম্বর ১৯৯০ থেকে ১ জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় পরিদর্শন করেন। এরপর ১৯৯১ সালের ২৩ মে লন্ডনের হাউস অব লর্ডস ভবনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন LIFE IS NOT OURS নামে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের শরণার্থী শিবির সরেজমিন পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে করে জুম্ম জনগণের উপর সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিষ্কার হয়ে উঠে।
১৯৯৬ সালের ২৩ অক্টোবর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক রেজুলিউশনে সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতল সরিয়ে নিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করে। ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলাদেশ সরকার তীব্র চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এতে করে আন্দোলনরত জুম্ম জনগণের শক্তি ও সাহস আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।
জুম্মদের উপর অব্যাহত গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, নির্বিচারে ধর-পাকড় ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার এবং সশস্ত্র আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসেবে জুম্ম ছাত্র সমাজের দেশপ্রেমিক অংশের মধ্যেও সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা-চরিত্র হতে থাকে। আশি দশকের শেষ প্রান্তে স্বৈরশাসক এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সারাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হওয়ায় সশস্ত্র আন্দোলনের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৮৯ সনের ২০ মে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুম্ম ছাত্র সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর জন্ম হয়। এর ফলে সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে সমন্বয় রেখে পিসিপি’র নেতৃত্বে দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন এগিয়ে যেতে থাকে। জুম্ম ছাত্র সমাজ পিসিপি’র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।
১৯৯০ সালে গঠিত হয় পাহাড়ি গণপরিষদ। এর আগে ১৯৮৮ সালে ৮ মার্চ সত্তর দশকের জুম্ম নারী সমাজের জাগরণের ধারাবাহিকতা হিসেবে “হিল উইমেন্স ফেডারেশন” নামে একটি জুম্ম নারী সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। পাহাড়ি গণপরিষদ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাশাপাশি হিল উইমেন্স ফেডারেশন গণতান্ত্রিকভাবে তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবেই হিল উইমেন্স ফেডারেশন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ি গণপরিষদের মাধ্যমে জুম্ম ছাত্র-জনতা-নারী সমাজের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। একাধারে সশস্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে।
দেশের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটা জাতীয় ইস্যু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের উপর বছরের পর বছর ধরে নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ও সোচ্চার হতে থাকে। ১৯৯২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতিদান, এতদাঞ্চলের সংঘটিত গণহত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ঘটনাবলীর তদন্ত, পাহাড়ি রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান, সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রশাসনসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যান্য দাবিসমূহ মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।
(চলবে…..)