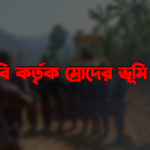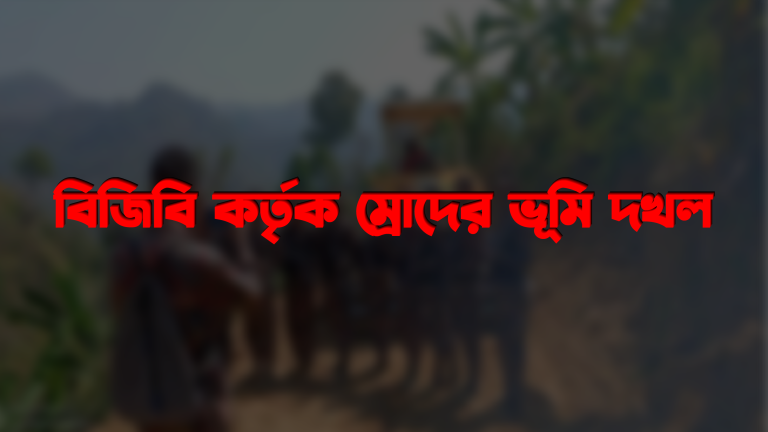মিতুল চাকমা বিশাল
শান্তিবাহিনী! একটি নাম, একটি স্বপ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভালোবাসার প্রাণের প্রিয় সশস্ত্র সংগঠন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি সামরিক সংগঠন এটি। যার নেতৃত্বে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পার্টি ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’।
জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠা নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও, এটিই সত্য যে, এই সংগঠনের জন্ম ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে হয়েছিল। কেননা ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ জনসংতি সমিতি তার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে, যেখানে আহ্বায়ক হিসেবে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নাম উল্লেখ দেখা যায়। পার্টির প্রতিষ্ঠার পরের বছরে, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের আজকের এই দিনে অর্থাৎ ০৭ জানুয়ারি জুম্ম জনগণের ‘গণমুক্তি ফৌজ’ গঠন করা হয়, যা কালেক্রমে জুম্ম জনগণের মুখে মুখে এটি ‘শান্তি বাহিনী’ নামে অত্যাধিক পরিচিতি লাভ করে এবং গণমুক্তি ফৌজ নামের বদলে সেই নামটিই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাহিনী নেহাতই কোনো অস্ত্রধারীদের কতিপয় সংগঠন নয়। এটি সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের সশস্ত্র সংগঠন। যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে অস্ত্রকে হাতে তুলেছিল। আজ জনসংহতি সমিতি আছে, তার বিভিন্ন রাজনৈতিক শাখা সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং অঙ্গ সংগঠনও আছে, কিন্তু শান্তিবাহিনী নেই।
পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেণি আবির্ভাবের সাথে সাথে শ্রেণিসংগ্রামেরও উদ্ভব ঘটে। ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় এবং শ্রেণি ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব অনুসারে এই সংগ্রাম কখনও সশস্ত্র, কখনওবা নিরস্ত্রভাবে চলমান ছিল, এখনও আছে। এমনকি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামেও বেঁচে থাকার তাগিদে এবং জন্তু জানোয়ারদের থেকে আত্মরক্ষার্থে মানুষ পাথর, তীর-ধনুককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমরা ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লবের কথা জানি। যারা একইসাথে জারতন্ত্র-সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনকারী কুকুরদের বিরুদ্ধে অসম এক লড়াই পরিচালনা করেছে এবং সফল হয়েছে। এই লড়াইগুলোও পরিচালিত হয়েছিল স্বশস্ত্রভাবে। তাছাড়াও বিশ্বের বহুদেশের নিপীড়িত জনগণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় অস্ত্র ধরে নিজেদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে সাঁওতালদের হুল বিদ্রোহ, নেতাজি সুভাষ বসুর স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে নেওয়া এবং অধূনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে লড়াই করা, এসবই কোন অপরাধমূলক কাজের অংশ ছিল না। বরং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এইসমস্ত সামরিক কার্যকলাপগুলো করা হয়েছিল, যদিও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের কাছে সেগুলো ছিল অপরাধ, বিদ্রোহ। কেননা শাসকগোষ্ঠী ছিল বরাবরই সশস্ত্র, হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং অগণতান্ত্রিক। অতএব, একটি সশস্ত্র, হিংস্র, নিষ্ঠুর এবং অগণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই একটি সশস্ত্র সংগঠনের প্রয়োজন।
১৯৭১ সালে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ভারতীয় উপমহাদেশের বুক চিরে যে লাল-সবুজের বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকশ্রেণি ঐতিহাসিকভাবে শোষিত ও বঞ্চিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় নি। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে আপন সংস্কৃতি, আপন ইতিহাস ও আপন ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয় নি। গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের অধিকারগুলো লিপিবদ্ধ করে শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি-দাওয়া আকারে পেশও করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের সরকার কোনরূপ কর্ণপাত করে নি। বরং উল্টো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালি জনগণের সাথে বাঙালি হয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছিল এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালিকরণ করা হবে বলে হাতের তুড়ি মেরে মেরে হুমকি প্রদান করা হয়েছিল। অপরদিকে ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়নের অংশ হিসেবে রুমা, আলিকদম ও দিঘীনালায় স্থাপন করা হয় ৩টি ক্যান্টনমেন্ট। ফলশ্রুতিতে বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগের পদ্ধতিতে অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে স্বাগত জানাতে হলো এবং জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে তৎপর একটি অধিকারকামী সশস্ত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আর সেই সংগঠনটিই হচ্ছে ‘জুম্ম গণমুক্তি ফৌজ’ বা শান্তিবাহিনী।
শান্তিবাহিনীর ১ম ব্যাচে ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা হলেন, প্রশান্ত কুমার চাকমা (জুলু), পরিমল চন্দ্র চাকমা (পাভেল), গৌতম কুমার চাকমা (অশোক), সুদত্ত চাকমা (রক্সিও), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন), প্রভাত কুমার চাকমা, ভদ্রসেন চাকমা, টন্টুমণি চাকমা, সুজিত চাকমা ও জোগেন্দু চাকমা।
দ্বিতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেন ১৩ জন। তারা হলেন, রূপায়ণ দেওয়ান (রিপ), ঊষাতন তালুকদার (সমীরণ), বিজয় সিংহ চাকমা (সুজয়), লক্ষী প্রসাদ চাকমা (দেবাশীষ), তাতিন্দ্রলাল চাকমা (পেলে), ধীর কুমার চাকমা (দেওয়ান), সূধন চাকমা (সরজিৎ), বিভূ রঞ্জন চাকমা (দীপু), চাবাই মগ (মংহ্লাউ), বকুল চন্দ্র চাকমা, রনবীর চাকমা, ভগবান চন্দ্র চাকমা (গড) ও ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ)।
তৃতীয় ব্যাচে প্রশিক্ষণ নেন প্রায় ৩০-৪০ জন। যাদের মধ্যে ছিলেন, কালী মাধব চাকমা (মিহির), অমিয় সেন চাকমা (কাঞ্চন), বিজয় বিকাশ চাকমা (বিবিসি), বিনয় কান্তি চাকমা (কৃঞ্চ), বিনোদ বিহারী খীসা (আদি), স্নেহ কুমার চাকমা (সজীব), রাম কিশোর চাকমা (শংকর), জাপানী রঞ্জন চাকমা (বিকাশ), হরিকৃষ্ণ চাকমা (বিদ্যুৎ), জয়েস, প্রলাশ চন্দ্র চাকমা (বিলাস), জ্যোতি বিকাশ চাকমা (রতন), আতশী মগ (রাহুল) ও রুপেশ প্রমুখ।
একইভাবে ছাত্রী জীবনের রঙিন আর স্বপ্নময় জীবন ছেড়ে নিরাপদ ভবিষ্যতের হাতছানিতে লেখাপড়া ছেড়ে জঙ্গল জীবনকে আঁকড়ে ধরে ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন উমে মং মারমা, দীপ্তি চাকমা, যুথিকা চাকমা, জয়শ্রী দেওয়ান, মায়ারাণী চাকমা, জড়িতা চাকমা, ভেলুয়া চাকমা সহ মহিলা সমিতির মোট ৩৫ জন। যারা সশস্ত্রভাবে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও প্রায় সবরকমের হাতিয়ার পরিচালনায় তাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ এবং সাংগঠনিক কাজে তারা ছিল একেবারে তুলনাহীন।
উমে মং-এর ভাষায় ‘একথা ঠিক যে, আমার হাতে অস্ত্র ছিল না। আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিনি। তবে আমাদের মহিলা সংগঠনের কর্মীরাও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। আসলে কি জানেন, যে কোন যুদ্ধেই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, সমর্থন খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সাধারণ মানুষকে মোটিভেট করতে হয়। সংগঠিত করতে হয়। কেন এই যুদ্ধ-সেটা বোঝাতে হয়। এই কাজটি করার জন্যেই আমাকে চলে যেতে হলো আত্মগোপনে।’ আরো সহজ কথায় তিনি বলেন, ‘এ জীবন যে কতটা কঠিন সেটা পুরোপুরি জেনেই আমি যাবার (শান্তিবাহিনীতে) জন্য মনস্থির করেছিলাম। শুধু আবেগতাড়িত হয়ে, না বুঝে যাই নি।’
পার্টির সামরিক কমিশনের অধীনে একটি জেনারেল হেডকোয়ার্টার ছিল এবং এই জেনারেল হেডকোয়ার্টার বা জিএইচকিউ এর অধীনে ৩টি সামরিক কোম্পানি ও ২টি আঞ্চলিক (বেসামরিক) কমান্ড সৃষ্টি করা হয়। আঞ্চলিক কমান্ডের কাজ ছিল পার্টির সাংগঠনিক কাজকে এগিয়ে নেওয়া অর্থাৎ পার্টির নীতি-আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আন্দোলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। সহজ কথায় জনসংহতি সমিতির আন্দোলন কেন? জনগণের সাথে এই আন্দোলনের সম্পর্ক কি? সেগুলো ব্যাখ্যা করা। রাজনৈতিক ভাষায় যেটাকে বলা হয়, জনগণের রাজনৈতিক সক্রিয়করণ। প্রতিক্রিয়াশীলকে নিস্ক্রিয় করা, নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করা এবং সক্রিয়কে অধিকতর সক্রিয় করা। অপরদিকে সামরিক কমান্ডের কাজ হচ্ছে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা অর্থাৎ আঞ্চলিক কমান্ড তথা পার্টির রাজনৈতিক কাজটিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করা। রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কাজগুলো যেখানেই বাধাগ্রস্ত হবে, সেখানেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুর বুকে কাঁপন ধরিয়ে কাজগুলোকে এগিয়ে নেওয়া সামরিক কমান্ডের কাজ। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া জরুরী যে, সামরিক কমান্ড কেবল যুদ্ধই করে না, তারা একইসাথে রাজনৈতিক সক্রিয়করণের কাজটিও চলমান রাখে। আর এটিই জনসংহতি সমিতির বিশেষত্ব এবং এটিও বিশেষভাবে স্মতর্ব্য যে, আঞ্চলিক এবং সামরিক উভয় কমান্ডের সদস্যরা কিন্তু সকলেই সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শান্তিবাহিনীর সদস্য। বিশেষ এই যে, সেই সময়ে জনসংহতি সমিতি বলতে শান্তিবাহিনীকেই বোঝানো হতো। অর্থাৎ শান্তিবাহিনী মানেই জনসংহতি সমিতি এবং জনসংহতি সমিতি মানেই শান্তিবাহিনী।
শান্তিবাহিনীর এই কাঠামো নিঃসন্দেহে একদিনে গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে নানা কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবেই এই কাঠামো গড়ে উঠেছিল। প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ২টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়, উত্তর অঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল। কর্ণফুলি নদীকে উক্ত দুই অঞ্চলের সীমানা ধরা হয়। উত্তরাঞ্চলের অধীনে ১, ২ ও বিশেষ সেক্টর এবং দক্ষিণাঞ্চলের অধীনে ৪, ৫ ও ৬নং সেক্টর। প্রত্যেকটি সেক্টরকেই আবার কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়। এই জোনের পরিচালনায় থাকেন ১জন জোন কমান্ডার, যার সামরিক পদবী ছিল ‘মেজর’। পরবর্তীতে দুটি অঞ্চলকে ৩টি কমান্ড পোস্ট, কমান্ড পোস্ট ‘এ’, কমান্ড পোস্ট ‘বি’ ও কমান্ড পোস্ট ‘এস’ নাম দেওয়া হয় এবং সেক্টর ও জোনের পরিবর্তে ‘ডিস্ট্রিক্ট এবং এরিয়া’ নামকরণ করা হয়।
অপরদিকে পার্টির সামরিক কমান্ডের অধীনে ছিল ৩টি কোম্পানি, ই-কোম্পানি, এফ-কোম্পানি ও বিশেষ কোম্পানি। প্রত্যেক কোম্পানির দায়িত্বে থাকতেন কোম্পানি কমান্ডার, যার পদবী ছিল মেজর। এই কোম্পানির অধীনে থাকত প্লাটুন, আবার প্লাটুনের অধীনে থাকত সেকশন। সেকশন হচ্ছে শান্তিবাহিনীর সর্বনিম্ন স্তরের কাঠামো। সাধারণত ৭-৮ জন সামরিক সদস্য নিয়ে একটি সেকশন গঠিত হতো, ৪টি সেকশন নিয়ে ১টি প্লাটুন এবং ৪টি প্লাটুন নিয়ে ১টি কোম্পানি গঠন করা হতো। যদিওবা অবস্থা বিশেষ এই কাঠামোর গঠন বিন্যাস পরিবর্তিত হতো। এছাড়াও পার্টির কাছে ছিল একটি সুবিশাল মিলিশিয়া বাহিনী। যারা একইসাথে সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। শান্তিবাহিনীর পাশাপাশি এই সুবিশাল মিলিশিয়া বাহিনীর অবদান জুম্ম জনগণের আন্দোলনে অনস্বীকার্য।
শান্তিবাহিনী প্রথম আক্রমণে যায় ১৯৭৬ সালের ১৯ জুন। বিলাইছড়ির ফারুয়া পুলিশ ক্যাম্প হামলা করে শান্তি বাহিনী তার আবির্ভাব বার্তা দেয় শাসকগোষ্ঠীকে। চাবাই মগ (মংহ্লাউ), মেজর প্রশান্ত কুমার চাকমা (জুলু) ও মেজর স্নেহ রঞ্জন চাকমা (ধ্রুব)-এর নেতৃত্বে ঐ আক্রমণ সংঘঠিত হয়। একই বছরের ০৯ আগস্ট বেতছড়িতে পুলিশের একটি টহল দলের উপর হামলা চালানো হয়। ১৯৭৭ সালের ৬ মে আলিকদমের কালামাঝি নামক স্থানে সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করা হয়। এভাবে পরপর শান্তিবাহিনীর গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুর উপর আক্রমণ করতে থাকে।
শান্তিবাহিনীর অধিকাংশ কমান্ডাররাই ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ছাত্রনেতা কিংবা সাধারণ ছাত্র। যাদের অধিকাংশই পড়ালেখা শেষ না করে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিজেদেরকে সপে দিয়েছিলেন অকাতরে।
তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, এফ কোম্পানির কমান্ডার মেজর লক্ষীপ্রসাদ চাকমা (দেবাশীষ)। যিনি রাঙামাটি সরকারি কলেজে বিএ পড়া অবস্থায় লেখাপড়া ছেড়ে চলে যান শান্তিবাহিনীতে। তারও স্বপ্ন ছিল, লেখাপড়া শেষ করে ভালো একটা চাকরি করার। দেশ গঠনে ভূমিকা রাখার। কিন্তু রাষ্ট্র সে সুযোগ তাকে দেয় নি।
তার কথায়, ‘প্রতিটি মানুষের জীবনের একটা দর্শন থাকে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমারও একটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল। আমি একদিন উচ্চ শিক্ষিত হবো। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবো। সংসারের দায়িত্ব পালন করবো। মা-বাবার সেবা করবো। স্বপ্ন তো স্বাভাবিক জীবনেরই ছিল।’ কিন্তু চলমান বাস্তবতা তাকে ঘরে থাকতে দেয় নি। শান্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ঘটনাটা তিনি বললেন এভাবে, ‘পরিবারের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে জাতির অধিকার আদায়ের দায়িত্বটা তখন আমার কাছে অনেক বড় মনে হলো। তাই পরিবারের কাউকে কিছু না বলে একদিন চলে গেলাম শান্তিবাহিনীতে।’
ছাত্রজীবন থেকে পড়াশোনা শেষ না করে এভাবে শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, নীলচন্দ্র চাকমা (কান্ত), বীরেন্দ্রলাল চাকমা (তঞ্চঙ্গ্যা), কমল বিকাশ চাকমা (দৈবারিক), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন), নীতিশ দেওয়ান (রোজার), মনিস্বপন দেওয়ান (রাজেশ), সুদত্ত চাকমা (রক্সিও), তাতিন্দ্রলাল চাকমা (পেলে) সহ আরো অনেকেই।
শান্তিবাহিনী গঠনের পর হতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠে এর সংগঠন ও বিন্যাস। শান্তিবাহিনীর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, যুব সমিতি ও আঞ্চলিক পরিচালকেরা এই প্যারালাল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং পরিচালনা করতেন। শান্তিবাহিনী ছিল নিরাপত্তা রক্ষার্থে এবং অন্যান্য কাঠামোগুলো ছিল সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ে গড়ে ওঠে বাংলাদেশ সরকারের প্যারালাল একটি সরকার। এই সরকার বাংলাদেশের সরকারের মতন অগণতান্ত্রিক ও দূর্নীতিগ্রস্ত নয়। এই সরকার জনগণেরই সরকার এবং এই সরকারের উপর জনগণের ছিল পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা। যার কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক নানা সমস্যার জন্য তারা শান্তিবাহিনীর কাছেই ছুটে আসত। কারণ শান্তিবাহিনীই তাদের নিরাপত্তা দিত ও সমস্যার সমাধান দিত। সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী কোথায়, কোনদিকে যাচ্ছে, কি করছে, না করছে সমস্ত তথ্য শান্তিবাহিনীর কাছে আসত। এমনকি ছুটিতে যাওয়া কিংবা কাজের জন্য যাওয়া অনেক শান্তিবাহিনীর সদস্যকে নিজেদের ঘরের মানুষ বলে সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছে জনগণ। এমনও নজির ছিল যে, সেনাবাহিনীরা একটি গ্রামে এসে একজন সন্তানসম্ভবা নারীকে বেদম মারধর করেছিল এবং জানতে চেয়েছিল শান্তিবাহিনীরা কোনদিকে গেছে। কিন্তু সেই নারীটি কিছুতেই মুখ খুলেন নি। এতটাই ভালোবাসা ছিল শান্তিবাহিনীর প্রতি। কারণ শান্তিবাহিনী কেবল একক কোনো বাহিনী নয়, এটি জনগণের বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। যেকারণে আজও শান্তিবাহিনীর সেই বীরত্বপূর্ণ সময়কে পার্বত্য এলাকায় ‘শান্তিবাহিনীর আমল’ বলা হয়। এতটাই প্রভাব ছিল শান্তিবাহিনীর।
শান্তিবাহিনীর শান্তিপ্রিয় সেই লড়াকু সদস্যরা স্বাভাবিক জীবনের আশায় অস্ত্র ছেড়েছিল বটে, কিন্তু শান্তি এখনও ফিরে আসে নি। ১৯৯৭ সালে যে আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্ন নিয়ে শান্তিবাহিনীরা তাদের কাঁধের অস্ত্রগুলো জমা দিয়েছিল একে একে, সেই আশা এখনও পূরণ হয় নি। স্বাভাবিক জীবনের বদৌলতে বরং প্রতিনিয়ত তাদেরকে অনিরাপদ এবং অনিশ্চয়তার জীবন কাটাতে হচ্ছে। চুক্তির ২৫ বছর পরেও শান্তির সুবাতাস পার্বত্য চট্টগ্রামে বইতে পারে নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আবহাওয়া আজ বড়ই শ্বাসরুদ্ধকর। নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেওয়ার বাস্তবতা এখন আর পাহাড়ে নেই। চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে সরকারের এই যে গড়িমসি, এ যেন সরাসরি উল্টোপথে যাত্রা। সত্যি বলতে এখনকার সময়ের পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি আর সেই ৭০-৮০ দশকের পরিস্থিতির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। বরং অত্যাচার আর শোষণের মাত্রাগুলো আরো ভিন্নররূপে, ভিন্ন আঙ্গিকে প্রয়োগ বিকশিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পাহাড়ে শান্তি এখন কার্যত অধরা। এমনিতর পরিবেশে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের জন্যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য ‘শান্তিবাহিনীকে’ তাই আবারো ফিরে পেতে হবে।
তথ্য সহায়িকা:
১. শান্তিবাহিনী, জিয়া হত্যা ও মনজুর খুন: মহিউদ্দীন আহমেদ
২. মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জীবন ও সংগ্রাম
৩. শান্তিবাহিনী গেরিলা জীবন: গোলাম মোর্তুজা